দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে নিয়মিত যে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল থাকে কম। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার, মূল্যস্ফীতি, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতে সাধারণ মানুষের পুরোপুরি আস্থা থাকে না।
এই আস্থাহীনতা দূর করা দরকার। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো থেকে উপস্থাপন করা দরকার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান। নতুবা যথাযথভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমরা যে গবেষণা করি, তার জন্যও দরকার হয় সঠিক পরিসংখ্যান।
নতুবা তার ফলাফল ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় না। অনেক সময় গবেষকরা তাঁদের বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি নির্মাণ করেন নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে। তবে তার পরিধি থাকে খুবই সীমিত। নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্ধারিত নমুনার ভিত্তিতে প্রণীত হয় ওই সব পরিসংখ্যান।
বৃহত্তর পরিসরে ও জাতীয়ভাবে তা অনেক সময় প্রযোজ্য হয় না। জাতীয়ভাবে প্রণীত পরিসংখ্যান মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ বা সংস্থা থেকে প্রকাশ করা হয়। তার ওপর প্রচ্ছন্নভাবে আধিপত্যমূলক প্রভাব থাকে ক্ষমতাসীন সরকারের। তারই ইঙ্গিতে কখনো পরিসংখ্যান হয় অতিরঞ্জিত, স্ফীত। আবার কখনো হয় কম মূল্যায়িত।
নিকট অতীতে এ ধরনের আলোচনা-সমালোচনা বরাবরই আমরা শুনে এসেছি।
বিগত সরকারের আমলে প্রায় ১৫ বছর ধরে নিয়মিতভাবে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে প্রায় ৬ থেকে ৮ শতাংশ। এর সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের উপলব্ধি তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তবে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো বরাবরই তাতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা ওই হিসাব থেকে এক থেকে দেড় শতাংশ পর্যন্ত কম অনুমান করেছে। দেশে বিদ্যমান জনজীবনের আর্থিক অবস্থা, ভোগ চাহিদা ও বিনিয়োগের পরিস্থিতি বিবেচনায় বিগত সরকার প্রদর্শিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অনেকের কাছেই অতি মূল্যায়িত মনে হয়েছে। এর ঠিক উল্টো অবস্থা আমরা লক্ষ করেছি মূল্যস্ফীতির হিসাব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। কাগজে-কলমে মূল্যস্ফীতির হার সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ৫-৬ শতাংশের মধ্যে। কখনো তা প্রদর্শন করা হয়েছে ৭-৮ শতাংশে। বাস্তবে তা অনেক সময় দুই ডিজিটও অতিক্রম করে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ও অনাস্থা ছিল প্রবল। গত জুলাই মাসে এই হার ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। অনেকে অনুমান করেছে ১৫ শতাংশেরও বেশি। একইভাবে সরকার বেকারত্বের হার কম দেখিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। বিভিন্ন হিসাবে তা দেখানো হয়েছে সাড়ে ৪ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশ। বেকারত্বের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত সংখ্যার কারণেও এই হারে কিছুটা তারতম্য ঘটেছে। তবে সাধারণভাবে দেশে বেকার মানুষের ঘনত্ব বিবেচনায় প্রদর্শিত হার অনেক কম বলে ধারণা করা হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিগত সরকার। জনতুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকটা বিফল হয়ে পুষ্পশোভিত পরিসংখ্যান দিয়ে জন-অসন্তোষ ঢাকতে চেয়েছে।
দেশের পণ্য উৎপাদন, চাহিদা এবং স্থিতির পরিসংখ্যান সম্পর্কে অতীতে সরকারের সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষি পরিসংখ্যানের কথা উল্লেখ করা যায়। অনেক সময় সরকারি ভাষ্যকে অতিকথন বলে মনে হয়েছে। প্রায়ই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রয়েছে। অথচ প্রায় প্রতিবছরই গড়পড়তা ৬০ থেকে ৭০ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে বিদেশ থেকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৯৮ লাখ মেট্রিক টন। স্বাধীনতার পর মোট আমদানির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টন। এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় আড়াই শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ১.২ শতাংশে। অন্যদিকে মোট খাদ্যশস্যের কথিত উৎপাদন এক কোটি টন থেকে বেড়ে হয়েছে পাঁচ কোটি টনেরও অধিক। অথচ খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ সে অনুপাতে হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি। এ ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের পরিসংখ্যান অতি মূল্যায়িত ভাবা অস্বাভাবিক নয়। অতি সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই স্ফীত; যে কারণে বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেক সময় পণ্যের সরবরাহ সংকট হেতু বাজার অস্থির হয়ে পড়ছে। পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। আমদানির আগাম প্রস্তুতি না থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
উদাহরণস্বরূপ ২০২৩-২৪ সালের আলু উৎপাদনের হিসাব সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে আলুর উৎপাদন ছিল এক কোটি ছয় লাখ টন। খাদ্য চাহিদা ও বীজ মিলে আমাদের বার্ষিক সর্বোচ্চ চাহিদা ৯০ লাখ টন। এতে ১৫-১৬ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু বাজারে অস্থিরতা ও আলুর মূল্যবৃদ্ধি দেখে ধারণা করা হয়েছে যে ওই পরিসংখ্যান অতিরঞ্জিত ও স্ফীত ছিল। কারণ বিদেশ থেকে আলু আমদানি করেও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো যায়নি। বাজারে আলু বিক্রি হয়েছে প্রতি কেজি ৭০ থেকে ৮০ টাকা। কোল্ড স্টোরেজগুলোতে অন্যান্য বছরে যেখানে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টন আলু সংরক্ষণ করা হতো, সেখানে গত অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ মিলেও ৩০ লাখ টন আলু মজুদ ছিল না।
পেঁয়াজের উৎপাদন বার্ষিক ৩৪-৩৫ লাখ টন বলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে দাবি করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯ লাখ মেট্রিক টন। আমাদের দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ২৬ থেকে ২৮ লাখ টন। তার পরও প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ছয়-সাত লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। অনেক সময় পেঁয়াজের দাম হয়ে পড়ে আকাশচুম্বী। ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হলে বাংলাদেশে এর আকাল নেমে আসে।
চালের উৎপাদন নিয়ে সব সময়ই বিভ্রান্তি বিরাজ করে। আমাদের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিশাল উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়। অনেক সময় আমদানি কম হলে সরবরাহ সংকটের কারণে চালের দাম বেড়ে যায়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমাদের চালের উৎপাদন ছিল চার কোটি সাত লাখ মেট্রিক টন। ১৭ কোটি ৩০ লাখ মানুষের জন্য বার্ষিক খাদ্য চাহিদা সর্বোচ্চ তিন কোটি ৭৩ লাখ টন। এতে উদ্বৃত্ত থাকার কথা ৩৪ লাখ টন চাল। কিন্তু বাজারের অস্থিরতা ও মূল্যবৃদ্ধি দেখে মনে হয়নি এই উৎপাদনের পরিসংখ্যান সঠিক। ইউএসএআইডির হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন হয়েছিল তিন কোটি ৭০ লাখ টন। অর্থাত্ বাংলাদেশের সরকারি তথ্য অনুসারে চালের উৎপাদন ৩৭ লাখ টন বেশি দাবি করা হয়েছিল। এ বছর আন্তর্জাতিক বাজারে চালের উচ্চমূল্যের কারণে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা আমদানিতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু গমের আমদানি ছিল রেকর্ড উচ্চতায় ৬৬ লাখ মেট্রিক টন।
২০২৪ পঞ্জিকা বর্ষের আমন চালের উৎপাদন এক কোটি ৭১ লাখ টন বলে দাবি করছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ। ইউএসএআইডি বলেছে, উৎপাদন হতে পারে এক কোটি ৪০ লাখ টন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পর পর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় রিমালের কারণে চালের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। দেরিতে চারা রোপণের কারণে হেক্টরপ্রতি ফলনও কম হয়েছে। কিন্তু তার প্রকৃত চিত্র কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যানে নেই। তবে সাম্প্রতিক অস্থির চালের বাজারের অবস্থা দেখে মনে হয় না যে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসাব সঠিক। বিবিএস এখনো এবারের আমন চাল উৎপাদনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। ওরা এত দেরি করে পরিসংখ্যান দেয়, যখন এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এর ওপর ভিত্তি করে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন পরিসংখ্যান নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। বর্তমানে দুধ, মাংস ও মাছের বার্ষিক উৎপাদন যথাক্রমে ১৪১, ৮৮ ও ৪৯ লাখ মেট্রিক টন। ডিমের উৎপাদন দুই হাজার ৩৩৮ কোটি। গত ১৫ বছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে দুধের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১২ শতাংশ, মাংসের ক্ষেত্রে ১৩ শতাংশ, ডিমের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ এবং মাছের ক্ষেত্রে সাড়ে ৩ শতাংশ। পণ্যের উৎপাদনে এত বেশি প্রবৃদ্ধি যখন হয়, তখন পণ্যমূল্য এত বেশি বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়। কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যাড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে প্রদত্ত দৈনিক জনপ্রতি দুধ, মাংস, ডিম ও মাছ ভক্ষণের পরিসংখ্যানের সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের মিল নেই। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) মোট দুধ উৎপাদনের যে হিসাব দিচ্ছে, সে অনুযায়ী দৈনিক জনপ্রতি দুধের প্রাপ্যতা ২২৫ গ্রাম। অথচ বিবিএসের তথ্য মতে, জনপ্রতি দুধের ভোগ মাত্র ৩৪ গ্রাম। ডিএলএসের তথ্য মতে, মাংসের প্রাপ্যতা জনপ্রতি ১৪০ গ্রাম, ডিম ১৯ গ্রাম, মাছ ৭৯ গ্রাম এবং মাছ-মাংস মিলে ২১৯ গ্রাম। বিবিএসের তথ্য মতে, মাংসের ভোগ ৪০ গ্রাম, ডিম ১৩ গ্রাম, মাছ ৬৮ গ্রাম এবং মাছ-মাংস মিলে ১০৮ গ্রাম। দুটি পরিসংখ্যানের মধ্যে বিশাল ফারাক।
ডিএলএসের তথ্যে মনে হয়, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন জাতীয় চাহিদার একান্ত কাছাকাছি, যা খুবই ভালো। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এসব পণ্যের দাম এত বেশি কেন? পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যখন ডিমের দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি পিস ছয় টাকা, তখন সেটি এখানে ১৪-১৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। দুধের দাম পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি। বর্তমানে প্যাকেটজাত দুধ প্রতি লিটার ১০০ টাকা, প্রায় এক ডলার। এটি বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বেশি। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে উৎপাদন খরচ আমাদের চেয়ে অর্ধেক। তারা সারা বিশ্বে সরবরাহ করছে দুধ। ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন খরচও বাংলাদেশে বেশি। ব্রাজিল ৫০০ টাকার কমে এক কেজি মাংস বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাহলে তাদের উৎপাদন খরচ আরো কম। আর বাংলাদেশে ৮০০ টাকার বেশি দামে প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের উৎপাদন খরচ কমানোর উপায় হচ্ছে দক্ষভাবে আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা। প্রডাকশন স্কিল বাড়ানো। সে জন্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা দরকার।
বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রদানের রাষ্ট্রীয় সংস্থা হচ্ছে বিবিএস। এই সংস্থাটির কাছ থেকে সঠিক পরিসংখ্যান প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু সংস্থাটির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না-ও হতে পারে। সে কারণে সংস্থাটিকে একটি স্বতন্ত্র ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে হবে। নির্মোহভাবে কাজ করে তাঁদের জাতির সামনে সঠিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। বিভ্রান্তিকর, অতি মূল্যায়িত ও অবমূল্যায়িত তথ্য প্রদান থেকে তাঁদের বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় সঠিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।
লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ












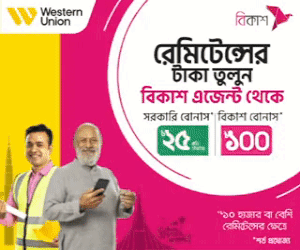





 Users Today : 22
Users Today : 22 Users Yesterday : 31
Users Yesterday : 31 Views Today : 191
Views Today : 191 Total views : 19120
Total views : 19120 Who's Online : 8
Who's Online : 8